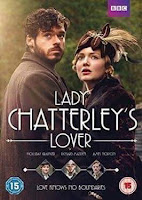২৩শে জুন, ১৭৫৭ সাল – পলাশীর যুদ্ধ-এ নবাব সিরাজউদ্দৌলা’কে হারিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি‘র সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলার রাজা হয়ে বসলেন।


ক্লাইভ চেয়েছিলেন এই বিজয় কে সেলিব্রেট করতে। কিন্তু তখনকার কলকাতায় না ছিল আজকের পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের মতন বিলাসবহুল হোটেল, না ছিল কোনো ‘ব্যাংকোয়েট হল’, না ছিল কোনো বড় গির্জা। ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া তো উৎসব তেমন জমে না! অগত্যা ক্লাইভ ঠিক করলেন যে তিনি ভিনদেশী দেবীর শরণাপন্ন হবেন।
এই যুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা ছিল অনেক – তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণদেব পলাশীর যুদ্ধের আগে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনশি; পরে হয়েছিলেন সুতানুটির তালুকদার – চার হাজারী মনসবদার। তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত শিক্ষক (প্রাইভেট টিউটর) হিসাবে – হেস্টিংসকে ফারসী শেখাতেন।
পলাশির যুদ্ধ জয়ের মোচ্ছব আজ বাঙালির জাতীয় উৎসব
পলাশীর যুদ্ধের ফলে নবকৃষ্ণের কপাল গেল খুলে। ক্লাইভের সঙ্গ দিয়ে মীরজাফর, রামচাঁদ রায়, আমীর বেগ, জগৎ শেঠ আর নবকৃষ্ণ প্রমুখরা মিলে সিরাজের কোষাগার লুঠ করে কোটি কোটি টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে নবকৃষ্ণ শুধুমাত্র ধনদৌলতই পান নি, সঙ্গে পেয়েছিলেন প্রভূত সন্মান আর ক্ষমতা।
১৭৬৬ সালে নতুন খেতাব পেয়ে নবকৃষ্ণ হলেন ‘মহারাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর’। পলাশীর রণাঙ্গনে মীরজাফর-এর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটলে সেদিন যাঁরা সবচেয়ে বেশি উল্লাসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতার নবকৃষ্ণদেব।
ক্লাইভ চেয়েছিলেন এই বিজয়কে সেলিব্রেট করতে।
———-
কিন্তু হিন্দুদের দেবীপূজা বসন্তকালীন দুর্গোৎসবের (বাসন্তীপূজা) তখন অনেক দেরি। ক্লাইভের পরামর্শে মুশকিল আসান করলেন নবকৃষ্ণদেব – বাসন্তীপূজাকে নিয়ে এলেন শরৎকালে। তবে নবকৃষ্ণ প্রথম অকালবোধন করেন নি। অতীতের বিভিন্ন গ্রন্থে নবকৃষ্ণের বহু আগে অকালবোধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এরমধ্যে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের অকালবোধন পূজা উল্লেখ্য (রামচন্দ্রের অকালবোধনকে বাদ রাখলাম, কারণ আসল রামায়ণ বা ঋষি বাল্মীকি লিখিত রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কোনো বিবরণ নেই, কৃত্তিবাস ওঝা লিখিত রামায়ণে আছে)। তাই নবকৃষ্ণ নিয়ম ভেঙে কিছুই করেন নি – তবে অকালবোধনের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই ভিন্ন ছিল।
ব্রিটিশদের নেকনজরে সিদ্ধিলাভ, দুর্গা পুজো শুরু হল শোভাবাজার রাজবাড়িতে
নবকৃষ্ণ যেন আলাদিনের প্রদীপ ঘষে তাঁর চকমিলান রাজবাড়ীর একদিকে গড়ে তুললেন ঠাকুরদালান, আরেকদিকে নাচঘর। সর্বত্র বসানো হল বিদেশি মার্বেল পাথর। এল ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, রৌপ্যখচিত আঁটাসোঁটা, খাসগেলাস ও নিশান, দেওয়ালে বিদেশি তৈলচিত্র আর সীতাহরণের উডকাট। গড়ে উঠল একচালা প্রতিমা। প্রতিমার গা-ভর্তি সোনার গয়না ঝলমল করে উঠল। দুর্গার কেশদামে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল ছাব্বিশটি স্বর্ণ নির্মিত স্বর্ণচাঁপা, নাকে তিরিশটি নথ, মাথায় সোনার মুকুট। প্রতিমা সাজাতে জার্মানি থেকে আনা হয়েছিল রাংতা। অশ্বপ্রতিম (গোধা) দুর্গার বাহনের গায়ে দেড়মাস ধরে সন্দেশের তবক বসানো হয়েছিল।
কৃষ্ণা-নবমীর দিন হয়েছিল বোধন। সেই থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত ব্রতী-ব্রাহ্মণেরা ঠাকুরদালানে বসে চণ্ডী, বগলা এবং বেদের সূক্ত পাঠ করেছিলেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় হয়েছিল বিল্ব-বরণ। সপ্তমীর সকালে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আসা দুই ‘স্কচ হাইল্যান্ডার ব্যান্ড’ নিয়ে গঙ্গায় কলাবউ স্নান করানো হয়েছিল। অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার শুভমুহূর্তে এক এক করে জ্বলে উঠেছিল একশো আটটি জাগ-প্রদীপ। তারপরে তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল সন্ধিপূজা – তখন ঠাকুরদালানে থিকথিক করছিল মানুষ।
দৈনিক নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছিল তেইশ মণ চালের, ভিয়েনে রান্না করা সত্তর-আশি রকমের ভোগের মিঠাই। বিশেষ পদ হিসাবে তৈরি হয়েছিল বড় কামানের গোলাকৃতি মতিচুর।
সে’বছর নবকৃষ্ণদেব আর নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে শরৎকালীন দুর্গাপূজার মাধ্যমে ইংরেজদের বিজয় উৎসবটি পালন করেছিলেন। শোনা যায়, নবকৃষ্ণ দেবের পূজা নাকি চলেছিল একশো দিন ধরে।
তত্ত্বজ্ঞদের মতে এর আগে শারদীয়া দুর্গাপূজার বিশেষ চল ছিল না, ছুটকো-ছাটকা দু’তিনটি উদাহরণ ছাড়া, ব্যাপকভাবে হত বাসন্তীপূজা। সেনযুগে রাজারাজড়া আর দস্যু-তস্করেরা এই পূজা করতেন বসন্তকালে। যুদ্ধজয়ের জন্য রামচন্দ্র শরৎকালে অকালবোধন করেছিলেন বলে যে কিংবদন্তি আছে, বাল্মীকি রামায়ণে তা অনুপস্থিত। তাহেরপুরের ভূঁইয়ারাজা কংসনারায়ণ মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে কিছু গ্রন্থে লিখিত আছে এবং জনশ্রুতি আছে, তবে তার সঠিক তথ্যপ্রমাণ নেই। ওদিকে আবার, রাজা সুরথ দুর্গাপূজা করেছিলেন চৈত্রমাসে, এখন যা বাসন্তীপূজা নামে খ্যাত। সুতরাং এই হিসেবে বলা যায় যে ক্লাইভই বঙ্গদেশে প্রথম জাঁকজমক করে শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তক।
মজার বিষয় হল ক্লাইভ নিজে খৃষ্টান ও মূর্তিপূজার বিরোধী হয়েও স্রেফ নিজের স্বার্থে ‘হিন্দু-প্রেমিক’ সেজে নবকৃষ্ণের দুর্গাপূজায় একশো এক টাকা দক্ষিণা আর ঝুড়িঝুড়ি ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজরা এ’দেশে দুর্গাপূজা কে উপলক্ষ করে গড়ে তুলেছিলেন এক অনুগ্রহজীবী তাঁবেদার সম্প্রদায়। নবকৃষ্ণের কাছেও দুর্গাঠাকুর ছিলেন উপলক্ষ মাত্র – ক্লাইভকে তুষ্ট করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। নবকৃষ্ণের দুর্গাপূজাকে অনেকে কোম্পানির পূজা বলে থাকেন। নবকৃষ্ণই কলকাতার প্রথম বাঙালি যিনি একজন আসল সাহেবকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হাতির দাঁতের ওপর লেখা আমন্ত্রণ লিপিটি তিনি তৈরি করিয়েছিলেন ক্লাইভকে উদ্দেশ্য করেই। নবকৃষ্ণ ভালো করেই জানতেন মূর্তিপূজার বিরোধী খৃষ্টান ক্লাইভকে কেবলমাত্র দুর্গাঠাকুর দেখিয়েই মন ভরানো যাবে না। তাই বোধনের দিন থেকে সাহেবদের জন্য মদ্য-মাংস আর নাচ-গানের অঢেল আয়োজনও তিনি করেছিলেন।
ক্লাইভ হাতির পিঠে চেপে সঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পূজা দেখতে এসেছিলেন। ঠাকুর দালানের সামনে ছিল সাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি – সিঁড়ি বরাবর কারুকার্য করা একটি নির্দিষ্ট আসনে এসে বসেছিলেন ক্লাইভ, তাঁর পাশের আসনে বসেছিলেন নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর। রাজবাড়ীর মেয়েরা বসেছিলেন দালানের একপাশে চিকের ভেতরে কার্পেটের উপরে। পুরুষেরা ছিলেন চিকের বাইরে। ক্লাইভ সে’দিন পশুবলি সহ হিন্দুদের দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলিও দিয়েছিলেন। পূজার তিনদিন গভীর রাত পর্যন্ত মহাধুমধামের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত খানাপিনা-নাচগানের আসর চলেছিল। দেশওয়ালীদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল কবিগান, তর্জা আর মর্জিনা-আবদল্লা’র যাত্রাগানের। ক্ল্যারিওনেট বাজনার তালে-তালে সারা রাত মর্জিনার নাচ আর দর্শকদের ‘এনকোর-এনকোর’ রব আসর মাত করে দিয়েছিল।
শোভাবাজার রাজবাড়ীর পূজায় আমন্ত্রিত খৃষ্টান পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব, এই দুর্গোৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখে গিয়েছেন, “চকমিলান প্রাসাদের মাঝখানে উৎসব প্রাঙ্গণ। সামনে পূজামণ্ডপ, পূর্বদিকের একটি ঘরে সাহেবীখানার বিপুল আয়োজন। হিন্দু নর্তকীদের নাচগান চলছে। চারিদিক ঘিরে কোম্পানির বাঘাবাঘা সাহেব-মেম অতিথিরা কৌচে বসে মৌজ করে তা দেখছেন।” শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংসও নাকি নাচ দেখতে হাতির পিঠে চেপে এসেছিলেন।
পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজদের বদন্যতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় অতঃপর শহরে ও অন্যত্র শ্রেষ্ঠী মুৎসুদ্দি দালালরা পূজার নামে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামাঞ্চলের জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীরাও সেই আনন্দ-উল্লাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার রাজা-বাবুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল দুর্গোৎসবে সাহেব-সুবোদের কতটা খুশি করা যায় তা নিয়ে। বিপুল আড়ম্বর আর চূড়ান্ত আভিজাত্যের প্রতীক সেদিনের এই পূজার কলকাতা ইংরেজদের চোখে ‘পারফেক্ট প্যারাডাইস’ হয়ে উঠেছিল।
অবশ্য নবকৃষ্ণের আগে ১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার কলকাতায় প্রথম দূর্গাপুজার আয়োজন করেছিল। তবে ঐতিহাসিকদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে যদি জব চার্নককেই কলকাতার পত্তনকারী ধরা হয় তবে ১৬৯০ এর ২৪ আগস্ট হলো এই সাবেকী কলকাতার জন্মদিন। অতএব সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পুজোকে সেই অর্থে কলকাতার প্রথম পুজো বলা যাবেনা।